
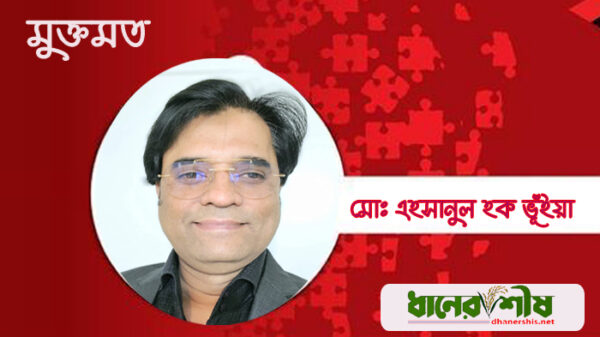

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট Donald J. Trump গত সেপ্টেম্বর’২৫ মাসে বাংলাদেশের জন্য নতুন রাষ্ট্রদূত হিসেবে ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনকে মনোনয়ন দিয়েছেন। এই মনোনয়ন ইতিমধ্যে United States Senate–এর ফরেন রিলেশনস কমিটিতে শুনানিতে উপনীত হয়েছে।
ক্রিস্টেনসেন বাংলাদেশ-সম্পর্কিত মার্কিন নীতিতে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হিসেবে দেখা হচ্ছে; তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়া, অর্থনৈতিক সম্ভাবনা, এবং দক্ষিণ এশিয়ার কৌশলগত অবস্থানের প্রসঙ্গ স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে।
সদ্য বাংলাদেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত তার বক্তব্যের মূল উপাদানগুলো বিশ্লেষণ করা হলো — বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, কূটনৈতিক বার্তা, অর্থনৈতিক নির্দেশনা ও ভূরাজনৈতিক বিষয়াদি।
একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী মুহূর্ত ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট
ক্রিস্টেনসেন তাঁর শুনানিতে স্মরণ করিয়েছেন যে, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন “বিগত দশকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যময়” হতে যাচ্ছে। তিনি বলেছেন, “The United States supports Bangladesh in its journey toward a bright and democratic future.”
এখানে দুটি বিষয়ে গুরুত্ব রয়েছে:
একদিকে, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের মধ্যে একটি নতুন রাজনৈতিক অধ্যায় দেখছে, যেখানে ক্ষমতায় থাকা দীর্ঘ সরকার পতনের পর পরিবর্তন এসেছে। তিনি সেটি সরাসরি উল্লেখ করেছেন — “student-led protests in August 2024 brought down a government that had been in power for 15 years.”
অন্যদিকে, এই মনোনয়ন ও বক্তব্যে রয়েছে পরবর্তী সরকারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের অংশীদারিত্বের আগ্রহ-সঙ্কেত। “…if confirmed … I look forward to … build strong ties with both the current Interim Government and its democratically elected successor”
বাংলাদেশ এই মুহূর্তে রাজনৈতিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে—যেখানে ১৫ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা সরকারের পরে একটি নতুন অবস্থার তৈরি হয়েছে। এখানেই যুক্তরাষ্ট্রের মনোযোগ ও আগ্রহ বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে।
যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক বার্তা ও ভীতি-সঙ্কেত-
ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনের ভাষণ স্রেফ শুভেচ্ছা বা সাধারণ রাষ্ট্রদূতের মন্তব্য নয়; এতে রয়েছে পরিষ্কার কূটনৈতিক ইঙ্গিত ও বার্তা।তিনি বলেছেন, বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে “its larger neighbours’ shadow”–এর মধ্যে রয়েছে। এটি সরাসরি ইঙ্গিত দেয় যে যুক্তরাষ্ট্র চায় না বাংলাদেশ এককভাবে কোনো বড় শক্তির প্রতিক্রিয়ায় বা প্রভাব-ক্ষেত্রের উপজীব্য হয়ে পড়ুক।
তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেছেন, বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্র “regional security and economic partnerships” শক্তিশালী করতে আগ্রহী।
সিনেট কমিটিতে তিনি চীনের সাথে বাংলাদেশের সামরিক সম্পর্ক প্রসঙ্গেও প্রশ্নের মুখে পড়েন—বিশেষ করে চীনের সাবমেরিন বেস ও জে-১০ যুদ্ধবিমানের সম্ভাব্য চুক্তি প্রসঙ্গে।
এখানে যুক্তরাষ্ট্রের চিন্তার দিক হলো: যদি বাংলাদেশ দীর্ঘমেয়াদিভাবে চীনের প্রতিরক্ষা সরঞ্জামে নির্ভর হয়ে পড়ে, তাহলে সেটি কৌশলগতভাবে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য উদ্বেগের বিষয় হতে পারে।
সংক্ষেপে, এই বক্তব্যগুলোর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র মূলত বলতে চাচ্ছে– বাংলাদেশ তাদের জন্য কেবল অর্থনৈতিক অংশীদার নয়, বরং একটি কৌশলগত মহুল্যবান ভূ-অঞ্চল। এজন্য তারা বাংলাদেশের নির্বাচন, নতুন সরকার এবং রাষ্ট্রীয় রূপান্তরের প্রতি সক্রিয় মনোযোগ দিচ্ছে।
অর্থনৈতিক ও বিনিয়োগ-সংক্রান্ত নির্দেশনা;
ক্রিস্টেনসেন শুধু রাজনৈতিক ও কৌশলগত প্রসঙ্গে কথা বলেননি—অর্থনীতিকভাবে তিনি স্পষ্টভাবে বলছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে ব্যবসা ও বিনিয়োগ বাড়াতে আগ্রহী। তাঁর বক্তৃতার মূল বিষয়গুলো হলো:
“Often referred to as one of the new Asian tigers, Bangladesh shows significant economic potential.”
তিনি বলেন—“If confirmed, I will work to promote opportunities for US business, reduce trade barriers … and strengthen US-Bangladesh economic ties.”
অর্থাৎ, যুক্তরাষ্ট্র মনে করছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দ্রুত প্রবৃদ্ধি, তার শ্রমশক্তি ও ভৌগোলেগিক অবস্থান যুক্তরাষ্ট্রের চোখে একটি স্ট্র্যাটেজিক অ্যাসেট।
একই সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন– বাংলাদেশের উপর রোহিঙ্গা বিষয়ক বোঝা রয়েছে এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারদের অংশগ্রহণ প্রয়োজন।
এখানে অর্থনৈতিক বার্তার মধ্যে রয়েছে একটা পরিষ্কার ইঙ্গিত—বাংলাদেশ যদি রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল ও নির্বাচনী ভিত্তিতে বিশ্বস্ত হয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র তার সঙ্গে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব বাড়ানোর জন্য প্রস্তুত রয়েছে।
নির্বাচনী প্রক্রিয়া, গণতন্ত্রীকরণ ও অস্থিরতা-ঝুঁকি;
বাংলাদেশের নির্বাচন ও রাজনৈতিক রূপান্তরের প্রসঙ্গে ক্রিস্টেনসেনের বক্তব্যের গুরুত্ব আরও স্পষ্ট হয়, কারণ:
তিনি পরবর্তী নির্বাচনের দিকে দেখছেন শুধু রাজনৈতিক পরিবর্তন হিসেবে না, বরং গণতান্ত্রিক রূপান্তর হিসেবে—“a bright and democratic future” ই দেখছেন।
নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে, তিনি বর্তমান অস্থায়ী সরকারের সঙ্গে এবং নতুন নির্বাচিত সরকারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের অংশীদারিত্ব বিবেচনায় নিচ্ছেন। এটি একটি কূটনৈতিক নিরাপত্তা-সঙ্কেতও—যে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য ও বৈধ হবে তা যুক্তরাষ্ট্র দেখছে।
তবে নির্বাচনের সঙ্গে ঝুঁকিও রয়েছে—রাজনৈতিক উত্তেজনা, মানবাধিকার বিষয়, নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। বাংলাদেশের জন্য এই মুহূর্তটি কার্যকরভাবে ব্যবহারের সুযোগ, কিন্তু সমান্তরালভাবে চ্যালেঞ্জও। যেমন, গত বছর ছাত্র-জনিত প্রতিবাদ থেকে রাষ্ট্রীয় স্তরে এনেছে বড় ধরনে প্রশ্নচিহ্ন।
এক অর্থে, ক্রিস্টেনসেনের বার্তা বলছে: বাংলাদেশ যদি এই নির্বাচনী সামর্থ্য ও রাজনৈতিক পরিবর্তনকে সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র তার সাথেই কাজ করতে প্রস্তুত। তবে সেই পথ স্বয়ংক্রিয় নয়—এখানে দায়িত্ব রয়েছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব-প্রক্রিয়া-নাগরিক সমাজের উপর।
কৌশলগত ভূমিকাঃ দক্ষিণ এশিয়া ও ইন্দো-প্যাসিফিক:
ক্রিস্টেনসেনের বক্তব্য আরও একটি বড় কোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ—তিনি বাংলাদেশের ভূগোল ও কৌশলগত অবস্থান নিয়ে বলছেন:
তিনি বলেছেন: “Bangladesh’s strategic location makes it an important participant in an open, secure, and prosperous Indo-Pacific region.”
এখানে দেখায় যে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে একরকম সন্ধিক্ষণ বা সেন্টারপয়েন্ট হিসেবে দেখছে, যেখানে শুধু দক্ষিণ এশিয়ার জন্য না, বরং ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।
চীন-ভারত-মিয়ানমার পাশাপাশি বাংলাদেশের ভূ–রাজনৈতিক অবস্থান যা আগে তুলনায় কম আলোচিত ছিল, এখন তা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি সুযোগ হিসেবে সামনে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্র চায় যাতে বাংলাদেশ একলা শক্তির প্রভাব বা নির্ভরতায় না পড়ে, এবং এমন অংশীদারিত্ব হয় যা বৃহত্তর অঞ্চলের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করবে।
এই ধারণা থেকে দেখা যায়—ক্রিস্টেনসেনের বক্তব্য কেবল দুই দেশীয় মেলবন্ধন নয়, বরং বহুপক্ষীয় কৌশলগত ফ্রেমওয়ার্কের অংশ।
বাংলাদেশের জন্য সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ
ক্রিস্টেনসেনের বার্তায় বাংলাদেশ-প্রেক্ষিতভাবে কয়েকটি সুযোগ ও চ্যালেঞ্জও স্পষ্ট হয়:
সুযোগগুলো:
বাংলাদেশ যদি আগামী নির্বাচনে সুশৃঙ্খল, পরিচ্ছন্ন ও অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে পারে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে আরও বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে দেখা যাবে।
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বিনিয়োগ ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে—যাকে বাংলাদেশ পথে লাগাতে পারে।
কৌশলগত অবস্থান থেকে, বাংলাদেশ একটি মিডল ইকোনমি রূপে উত্তরণ ও আঞ্চলিক স্থিতিশ-ভিত্তিক অগ্রগতির জন্য নিজেকে স্থাপন করতে পারে।
চ্যালেঞ্জগুলো:
নির্বাচনী প্রক্রিয়া যদি রাজনৈতিক উত্তেজনায় ঘেরা হয় বা মানবাধিকারের চ্যালেঞ্জ হয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে আলোচনায় নেতিবাচক ইঙ্গিত আসতে পারে।
প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি যেমন চীন বা ভারতের প্রতিক্রিয়া, বা নিরাপত্তা-প্রকল্পে অনেক দায়িত্ব বাংলাদেশের সামনে রয়েছে।
অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব বাড়াতে চাইলে, দেশকে অবশ্যই বাণিজ্য-বাধা, পরিবেশগত ও সামাজিক দায়বদ্ধতা, শ্রমনীতি ইত্যাদি বিষয়েও প্রস্তুত থাকতে হবে।
শেষ কথা:
ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনের মুহূর্তিক বক্তব্য বাংলাদেশের জন্য একটি কূটনৈতিক প্রতিশ্রুতি ও বার্তা। তিনি বলছেন—যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে ইতিমধ্যে লক্ষ করছে এবং আগামী রাজনৈতিক রূপান্তরকে যুক্তরাষ্ট্র একটি নতুন সম্ভাবনার হিসেবে দেখছে। দেশের জন্য এই মুহূর্ত একটি ক্রসরোড; রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা, নির্বাচন-সফলতা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও কৌশলগত অংশীদারিত্ব—সব মিলিয়ে বাংলাদেশের সামনে রয়েছে এক নতুন অধ্যায়।
তবে বার্তাটি শুধুই প্রশংসা নয়; এটি একটি আমন্ত্রণ—“আপনি যদি এই পথে যেতে চান, আমরা সাথেই আছি।” উত্তরটি এখন বাংলাদেশের নেতৃত্ব, রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ ও বেসরকারি খাতের উপর পড়েছে।
উল্লেখ্য যে,যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের ওয়েবসাইট অনুযায়ী, ২০১৯ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ক কাউন্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ক্রিস্টেনসেন।
— মোহাম্মদ এহছানুল হক ভূঁইয়া
প্রধান সম্পাদক, ধানের শীষ ডট নেট
www.dhanershis.net